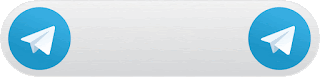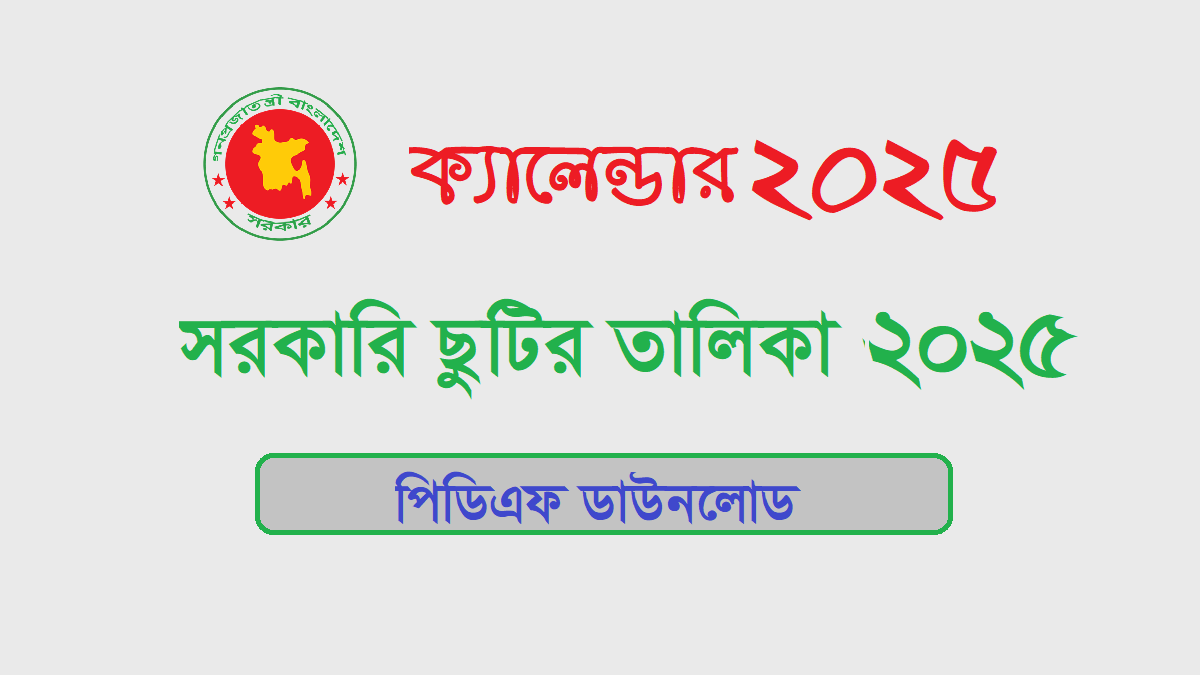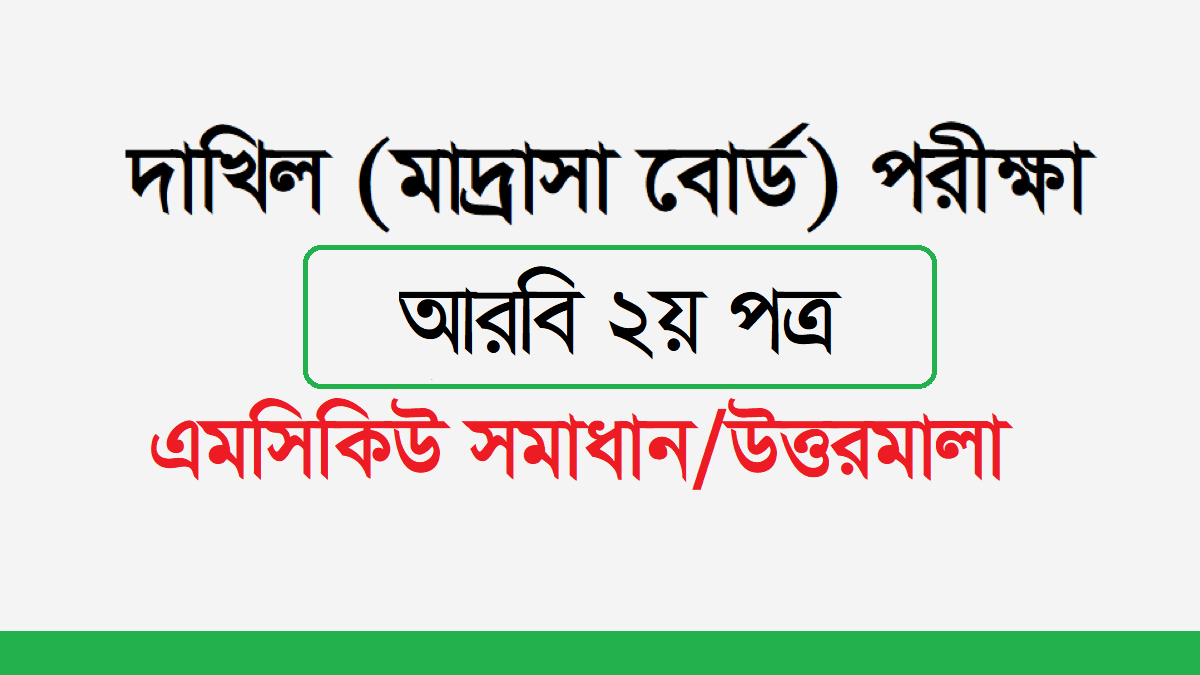বাংলা সাহিত্য (বাংলা : ৠং ৠহিত্য , রোমানাইজড : বাংলা শাহিত) বলতে বোঝায় বাংলা ভাষায় লেখার মূল অংশ । বাঙালির বিকাশ ঘটেছিল প্রায় 1,300 সালে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা হল চর্যাপদ , দশম এবং একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ মরমী গানের একটি সংকলন , এবং এটি বাংলা, অসমীয়া , ওড়িয়া এবং পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য ভাষার পৈতৃক ভাষায় রচিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
শাখা ইন্দো-আর্য ভাষার, বাংলা সাহিত্যের সময়কাল তিনটি যুগে বিভক্ত – প্রাচীন (650-1200), মধ্যযুগ (1200-1800) এবং আধুনিক (1800-এর পর)। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ (যেমন মঙ্গলকাব্য ), ইসলামী মহাকাব্য (যেমন সাইয়্যিদ সুলতান এবং আবদুল হাকিমের রচনা ), বৈষ্ণব গ্রন্থ (যেমন চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ), আরবি , ফারসি অনুবাদ সহ বিভিন্ন কাব্যিক ধারা রয়েছে । এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। এবং মুসলিম কবিদের ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ (উদাহরণস্বরূপ আলাওলের রচনা )।
উপন্যাস 19 শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল। ইস্টার্ন নাগরী লিপি ছাড়াওইতিহাসের কিছু অংশ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে বিভিন্ন লিপি যেমন পারসো-আরবি এবং সিলেটি নাগরী । নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কাজী নজরুল ইসলাম, তার সক্রিয়তা এবং ব্রিটিশ বিরোধী সাহিত্যের জন্য উল্লেখযোগ্য, একজন বিদ্রোহী কবি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃত।
1909 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম, প্রায় 1940.
প্রাচীন যুগ(650-1200)
চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি রাজশাহী কলেজের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে ।
বাংলা ভাষায় প্রথম রচনাটি 10 ম এবং 12ম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল । লুইপাদা, কানহাপাদা, কুক্কুরিপদ, চাতিলপাদা , ভুসুকুপাদা, কামলিপদ, ধেঁধনপাদ, শান্তিপদ ও শবরপদ ইত্যাদি। পাণ্ডুলিপিটি 1907 সালে বাঙালি ভাষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রয়্যাল কোর্ট লাইব্রেরিতে একটি তালপাতার উপর আবিষ্কার করেছিলেন। যেহেতু এই পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষা শুধুমাত্র আংশিকভাবে বোঝা গিয়েছিল, তাই শাস্ত্রী সেগুলি সন্ধ্যাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।(সন্ধ্যা) নামের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ, যার অর্থ সাধারণ ভাষা ।
মধ্যযুগীয় (1200-1800)
প্রারম্ভিক মধ্যযুগ / ক্রান্তিকাল (1200-1350)
এই সময়টিকে সেই সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয় যেখানে অনেকগুলি সাধারণ প্রবাদ এবং ছড়া প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। বাংলা বর্ণমালা অনেকটা বর্তমানের মত হয়ে উঠেছে। রামাই পণ্ডিত এবং হলুধ মিশ্র এই সময়ের উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন।
পূর্ব চৈতন্য (১৩৫০-১৫০০)
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি, যার পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহাম্মদ সগীর এবং কৃত্তিবাস ওঝার মতো লেখক ছিলেন।
মুসলিম লেখকরা ধর্ম, সংস্কৃতি, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেম এবং ইতিহাসের মতো কল্পকাহিনী এবং মহাকাব্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করছিলেন; প্রায়শই থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস এবং শাহনামেহের মতো আরবি ও ফার্সি সাহিত্যকর্ম থেকে অনুপ্রেরণা নেয় বা অনুবাদ করে।
সাহিত্যের রোমান্টিক ঐতিহ্যে শাহ মুহাম্মদ সগীরের ইউসুফ ও জুলেখার কবিতার পাশাপাশি সাবিরিদ খানের রচনাও দেখা যায়। দোভাষী সংস্কৃতি মুসলিম গল্পগুলিকে চিত্রিত করার জন্য বাংলা পাঠ্য এবং ফারসি শব্দভাণ্ডারে আরবিকে প্রবর্তন করে। মহাকাব্যের মধ্যে রয়েছে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, আবদুল হাকিম রচিত জঙ্গনামা এবং বারিদের রসুল বিজয় শাহ।
চণ্ডীদাস ছিলেন এই সময়ের একজন বিখ্যাত হিন্দু গীতিকার, যিনি জয়দেবের রচনাগুলিকে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য এবং রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের প্রতি নিবেদিত হাজার হাজার কবিতা যেমন শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনের জন্য বিখ্যাত। এই সময়ের অধিকাংশ হিন্দু লেখক বিদ্যাপতি নামে পরিচিত একজন জনপ্রিয় মৈথিলি ভাষার বৈষ্ণব কবি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। মালাধরা বসুর শ্রী কৃষ্ণ বিজয়া , প্রধানত ভাগবত পুরাণের 10 তম এবং 11 তম ক্যান্টোগুলির অনুবাদ, এটি প্রাচীনতম বাংলা আখ্যানমূলক কবিতা যা একটি নির্দিষ্ট তারিখে বরাদ্দ করা যেতে পারে। [৬] 1473 থেকে 1480 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত, এটি কৃষ্ণকথার প্রাচীনতম বাংলা আখ্যানমূলক কবিতাও। রামায়ণ , শ্রী রাম পাঁচালী শিরোনামে, অনুবাদ করেছেন কৃত্তিবাস ওঝা।
চৈতন্য যুগ (1500-1700)
লালন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, এবং অ্যালেন গিন্সবার্গ সহ অনেক কবি, সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিলেন।
এর পুনর্গঠনের পর আরাকানে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এটি আরাকানের রাজদরবারে সংরক্ষিত বিশিষ্ট লেখকদের বাড়ি ছিল, যেমন আলাওল, যিনি পদ্মাবতী লিখেছেন, সেইসাথে দৌলত কাজী, দৌলত উজির বাহরাম খান, কোরেশি মাগন ঠাকুর যিনি চন্দ্রাবতী এবং মর্দান লিখেছেন, যিনি নাসিরনামা লিখেছেন। দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজী ছিলেন প্রথম কবি। তিনি সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী লিখতে শুরু করেন, যা প্রথম বাঙালি রোম্যান্স বলে বিবেচিত হয়। আদালতে টিমওয়ার্ক ছিল সাধারণ, এবং আলোল কাজীর রোম্যান্সের অবসান ঘটায় কারণ কাজী রোম্যান্স সম্পূর্ণ করার আগেই আলোল মারা যান।
আধুনিক যুগ (1800-বর্তমান)
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম মহাকাব্য, তিলোত্তমা সম্ভাব কাব্য , 1860 সালে প্রকাশিত, প্রথম বাংলা কবিতা ছিল ফাঁকা ছন্দে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 19 শতকের শীর্ষস্থানীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ভারতের জাতীয় গান বন্দে মাতরমও লিখেছিলেন , যা তার উপন্যাস আনন্দমঠ (1882) এ পাওয়া যায়। 1880-এর দশকে চ্যাটার্জি তাঁর ধর্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত গ্রন্থে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে , ভগবদ্গীতার মতো হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে কৃষ্ণবাদের সমস্যাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন।
রমেশ চন্দর দত্ত এবং মীর মশাররফ হোসেন তাদের উপন্যাস রচনার জন্য উল্লেখযোগ্য। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সেই সময়ের প্রধান নাট্যকার, অন্যদিকে অক্ষয় কুমার বড়াল এবং রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তাদের প্রভাবশালী প্রবন্ধের জন্য বিখ্যাত। রাসুন্দরী দেবী 1876 সালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম সম্পূর্ণ আত্মজীবনী লেখেন।
প্রাক-ঠাকুর যুগেও জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি আন্ডারকারেন্ট দেখা যায় যা সমসাময়িক বাংলার দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে। গদ্যশৈলী, সেইসাথে এই রচনাগুলিতে হাস্যরস প্রায়শই নিস্তেজ, ভোঁতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল। এই বিষয়ে একটি মাস্টারপিস ছিল কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত “হুতোম পেচার নকশা” (একটি পেঁচার স্কেচ) এবং 19 শতকের কলকাতার “বাবু” সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে চিত্রিত করেছে। এই বিষয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল পীর চাঁদ মিত্রের “আলালের ঘোরের দুলাল” (দ্য স্পোয়েলড ব্র্যাট), ন্যায়মোহন তারাকালঙ্কারের “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকাল বঙ্গ সমাজ” (রামতনু লাহিড়ী এবং সমসাময়িক বাঙালি সমাজ), এবং “নব বাবু বিলাস” এবং ” ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব বিবি বিলাস”।
এই বইগুলি তর্কযোগ্যভাবে সমসাময়িক বাংলা উপভাষা এবং জনপ্রিয় সমাজকে কার্যকরভাবে চিত্রিত করেছে, এবং রূপচাঁদ পাখি এবং ভোলা ময়রার মতো অদম্য ব্যক্তিরা লিখেছেন, খের এবং কবিয়াল গানের মতো এখন বিলুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্রের ধরনও অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুর সংস্কৃতির উত্থান এবং বাঙালি সমাজে সাহিত্যের লালিত্য ও পরিশীলিততার ক্রমবর্ধমান পছন্দের পর থেকে এই ধরনের বই বিরল হয়ে উঠেছে।
বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।
বাংলা ভাষা আন্দোলনের বার্ষিকীতে শহীদ মিনার, ঢাকা প্রদর্শিত।
ভাষা মেমোরিয়াল, কলকাতা।
কায়কোবাদ একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক কবি ছিলেন।
হাসন রাজার কবিতা গ্রামবাংলায় আজও বিশিষ্ট।
বঙ্কিম, ঠাকুর, শরৎ ও নজরুল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী
কাজী নজরুল ইসলাম সিলেটে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে বসেন। নজরুলের অবদানের মধ্যে রয়েছে বাংলা গজলের ব্যাপক সমৃদ্ধি।
বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভারতে ব্যাপকভাবে সমাদৃত, যদিও তার উপন্যাস, বাংলাদেশে কম সম্মানিত, বাংলাদেশে কিছুটা জনপ্রিয়। [উদ্ধৃতি প্রয়োজন] বঙ্কিম মেমোরিয়াল পুরস্কার হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক। ঠাকুর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, জনগণ মন এবং বাংলাদেশের অমর সোনার বাংলা উভয়ের রচয়িতা, সেইসাথে শ্রীলঙ্কা মঠের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে নজরুলকে পালিত করা হয়।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস, উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। তিনি প্রবন্ধও লেখেন, যেগুলো সংকলিত হয়েছিল নাড়ির মুল্য (1923) এবং স্বদেশ ও সাহিত্য (1932) । শ্রীকান্ত, চারিহীন, দেবদাস, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা এবং পথের দাবী তাঁর জনপ্রিয় রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম।
ছোট গল্প লেখক
বাংলা সাহিত্যও ছোটগল্পের জন্য বিখ্যাত। কয়েকজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র।
1947-1965
রাজশেখর বসু (1880-1960) ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক। “পরশুরাম” ছদ্মনামে রচিত তাঁর গল্পে তিনি বাঙালি সমাজের বিভিন্ন অংশের হীনমন্যতা ও নীচতা নিয়ে মজা করেছেন। তার প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে: গদ্দালিকা (1924), কাজজাবলি (1927), হনুমানের স্বপ্ন (1937), গমনাষ জাতির কথা (1945), ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প (1952), কৃষ্ণকলি ইত্তাদি গল্প (1953), নীলতারা ইত্তাদি (1956 ) ), আনন্দীবাই ইত্তাদি গালপা (1958) এবং অলৌকিক ইত্তাদি গালপা(1959)। তিনি 1955 সালে পশ্চিমবঙ্গ কৃষ্ণকলি ইত্যদি গল্পের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার পান।
রাজশেখর একজন প্রখ্যাত অভিধানকার, অনুবাদক এবং প্রবন্ধকারও ছিলেন। তাঁর চলন্তিকা (1937) সবচেয়ে জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে একটি, যখন তাঁর মেঘদূত (1943), রামায়ণ (1946), মহাভারত (1949) এবং ভগবদ্গীতা (1961) এর বাংলা ভাষায় অনুবাদগুলিও প্রশংসিত। [২২] তার প্রধান প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে লাঘুগুরু (1939) এবং বিচিন্তা (1955)।
হাইপোথিসিস মুভমেন্ট
হাইপোথিসিস মুভমেন্ট, বিখ্যাত আমেরিকান সমালোচক, স্টিভ লেব্ল্যাঙ্ক কর্তৃক ‘একটি ছোট সাহিত্য বিপ্লব’ হিসাবে ব্র্যান্ডেড, কলকাতার ‘পুষ্ট’, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তার নতুন শৈলী কথাসাহিত্য, সারাবঙ্গ কবিতা এবং বিশ্বজনীনতাকে প্রচার করে চলেছে। ভট্টাচার্য চন্দনের নেতৃত্বে। , 1969 সালে শুরু হয়েছিল। এটি সম্ভবত ভারতের একমাত্র দ্বিভাষিক (বাংলা-ইংরেজি) সাহিত্য আন্দোলন, যা বাংলা সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেটি সুপরিচিত আন্তর্জাতিক অ্যাভান্ট-গার্ড লেখক এবং রিচার্ড কোস্টেলনেটজের মতো মেল শিল্পীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে তার ডানা ছড়িয়েছে। জন এম বেনেট, শিলা মারফি, ডন ওয়েব সহ উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবি, লেখক এবং শিল্পী যেমন ভাট্টাচার্জ চন্দন।
বিসিএস অথবা যেকোন সরকারী চাকরীর রিটেন এবং ভাইবা পরীক্ষার জন্য এই তথ্যগুলো জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।